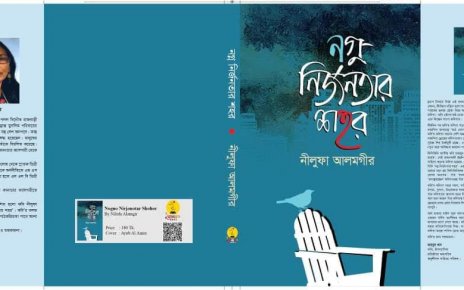১৯৯০-এর দশক। রবার্ট উইলিয়াম নামে মার্কিন এক গবেষক চাকরি করেন ফিলিপাইনের কৃষি বিভাগে। ফিলিপাইন তখন অনুনন্নত দেশ। চারপাশে ক্ষুধার্ত আর রুগণ মানুষের হাহাকার।
বিশেষ করে বেরি বেরি নামে এক ধরনের রোগ কাতারে কাতারে মানুষ মারছে। এই রোগ বড্ড যন্ত্রনাদায়ক। শরীর ফুলে ওঠে। পানি জমে।
শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। হাত-অবশ হয়। পা ভারী হয়ে ওঠে। ঝিন ঝিন লাগে।
শেষমেশ হার্ট ফেইল করে মারা যায় রোগী। উইলিয়াম ছোটবেলা থেকেই এই রোগের সঙ্গে পরিচিত। বাবার চাকরিরে সূত্রে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে দক্ষিণ ভারতে। ভারতেও তখন অভাব। ভাত-কাপড়ের অভাব, চিকিৎসার অভাব।
সেখানেও ছিল বেরিবেরি। বেরির আক্রান্তদের দুর্ভোগ তাই খুব কাছ থেকেই দেখেছেন উইলিয়ামস। ফিলিপাইনেও যখন একই অবস্থা দেখলেন, তখন ভাবলেন এই রোগের জন্য কিছু একটা করার কথা। শুরু হলো গবেষণা।
ফিলিপাইনের আরেকটা ব্যাপার উইলিয়ামসকে কষ্ট দিয়েছিল। সে দেশের অর্ধেক শিশুই মারা পড়ছিল বেরিবেরিতে।
প্রথমেই শুরু হলো পর্যবেক্ষণ। মধ্যযুগে অসুখবিসুখকে শুধুই শারীরিক সমস্যা বলে মনে করা হতো। এর পেছনে যে জীবাণুদের হাত থাকতে পারে এমনটা জানতেন না খোদ গবেষকেরাও। সেই ধারণার পরিবর্তন হয় তিনটি মানুষের কারণে–অ্যান্টোনি লিউয়েনহুক, এডওয়ার্ড জেনার ও লুই পাস্তুর।
পাস্তুরের গবেষণার পর বাস্তবতা সম্পূর্ণ উলটে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন, সকল রোগের পেছনেই আছে জীবাণুর কারসাজি। তাই নতুন কোনো রোগের চিকিৎসা করতে গেলে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতেন সেই রোগের জীবাণুর সন্ধান করার। উইলিয়ামসও সে পথে হাঁটতেন হয়তো। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরেকজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর অসমাপ্ত কাজ তার গবেষনার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়।
২.
গল্পের এ পর্যায়ে আরেকজন বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। আসলে তাঁকে বাদ দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম বড় আবিসষ্কারের গল্পটা বলা অন্যায় হবে। নাম তাঁর ক্রিশ্চিয়ান আইকম্যান। ডাচ এই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরও আগ্রহ ছিল বেরিবেরি নিয়ে। এ কারণেই এক মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় চলে যান।
আর সব বিজ্ঞানীদের মতো আইকম্যানও জীবাণুর পেছনে ছোটেন। বুঝতে পারেন, যদি শনাক্ত করা যায় বেরিবেরির জীবাণুটাকে তাহলেই কেবল টিকা আবিষ্কার সম্ভব। সুতরাং কাজে লেগে পড়েন আইকম্যান।
আইকম্যান গবেষণাগারে মুরগির ছানা পুষতেন। সম্ভবত লুই পাস্তুরের কাছ থেকে অণুপ্রাণীত হয়েছিলেন। পাস্তুর মশায় প্রথম টিকা আবিষ্কারে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করেন মুরগিকে।
আইকম্যান বেরিবেরি আক্রান্ত রোগীর শরীরের ক্ষতস্থান থেকে তরল পদার্থ সংগ্রহ করেন। ভেবেছিলেন যদি জীবাণু থেকে তাহলে এই তরলেও তার নমুনা থাকবে। করলেন পরীক্ষা। কিন্তু কোনো জীবাণুর সন্ধান পেলেন না। তবে আরেকটা কাকতালীয় ঘটনা ঘুরিয়ে দিল গবেষণার মোড়। ১৮৯৬ সালে তাঁর গবেষণাগারের মুরগিগুলো হঠাৎ করেই বেরিবেরিতে আক্রান্ত হলো। গণহারে। সুতরাং আইকম্যান আরেকবার সুযোগ পেয়ে গেলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার। তিনি অসুস্থ মুরগি থেকে বেরিবেরির নমুনা নিয়ে সুস্থ মুরগিদের শরীরে প্রবেশ করালেন। কাজ হলো না। কিছুতেই অসুস্থ হলো না সুস্থ মুরগিগুলো। তখন আইকম্যান নিশ্চিত হলেন, বেরিবেরি রোগের কারণ কোনো জীবাণু নয়।
তাহলে?
আবার সেই আকস্মিক ব্যাপার। হঠাৎ করেই অসুস্থ মুরগিগুলোর সুস্থ হয়ে উঠল!
কেন সুস্থ হয়ে উঠল, এবার সেই কারণ অনুসন্ধানে নামলেন আইকম্যান। রীতিমতো তদন্ত করে বের করে ফেললেন ঘটনা কী?
লাল চালের চেয়ে তখন সাদা চালের দাম বেশি। ইন্দোনেশিয়ার হাসপাতালগুলোতে উন্নতমানের খাবার ভেবে রোগীদের জন্য খাবার হিসেবে সাদা চাল বরাদ্দ ছিল। সব হাসপাতালেই বাবুর্চি থাকে। তিনি রোগিদের জন্য রান্নাবাড়া করেন। আইকম্যানের হাসপাতালের ওই বাবুর্চি রোগিদের জন্য বরাদ্দের সাদা চাল চুরি করে মুরগিদের খাইয়েছিল কিছুদিন। আর ওই সময়টাতেই মুরগিদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ দেখা দিয়েছিল।
আইকম্যান তখন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলেন। অনুমান করেন, সাদা চালে এমন কোনো খাদ্য উপাদানের ঘাটতি আছে যার অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। যতদিন লাল চাল খেয়েছে ততদিনে মুরগির শরীরে বেরি বেরি রোগ দেখা যায়নি। এর মানে হলো, নিশ্চয়ই লাল চালে সেই উপদানটা আছে?
সুতরাং বেরিবেরি এমন একটা রোগ যার পেছনে কোনো জীবাণু দায়ী নয়।
এখন প্রশ্ন হলো সেই খাদ্য উপাদানটা কী?
আইকম্যান হয়তো সেটা জানারও চেষ্টা করতেন। কিন্তু ততোদিনে তিনি চরম মাত্রায় অসুস্থা। তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে। বাধ্য হয়ে গবেষণা বাদ দিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে দেশে ফিরে গেলেন।
৩.
রবার্ট উইলিয়ামস জানতেন আইকম্যানের গবেষণার কথা। তিনি নিজেও লক্ষ্য করেছেন, ফিলিপাইনের সাধারণ মানুষের মধ্যে সাদা চালের ভাত খাওয়ার প্রবণতা বেশি। শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে একই কারণে। উইলিয়ামস লক্ষ করেছেন, যেসব শিশু বেরিবেরিতে মারা পড়ে তাঁদের বেশিরভাই মায়ের দুধ পান করে। তোলা দুধ নয়।
তারমানে মায়েরা সাদা চাল খাচ্ছেন, তারই ফলে দুধে সেই বিশেষ উপদানের ঘাটতি পড়ছে। বাচ্চারাও তাই সেই উপদানের অভাবে ভুগছে।
উইলিয়ামস আইকম্যানের অসমাপ্ত কাজে হাত দিলেন। শুরু করলেন লাল চাল আর সাদা চাল নিয়ে গবেষণা। সে সময় লাল চাল আর সাদা চালের মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধু ছাঁটাতেই। আজকালকার মতো প্রাকৃতিকভাবে তৈরি সাদা চাল ছিল না। ঠেঁকি ছাটা চাল তখন লাল হতো। কিন্তু মেশিনে বেশি করে ছাঁটা চালই সাদা রঙের হতো। তারমানে চালের ওপর যে লাল আবরণ—মধ্যেই রয়েছে বেরিবিরি রোগের সমাধান।
শুরু হলো উইলিয়ামসের গবেষণা। চালের লাল আবরণ আলাদা করে তার নির্যাস তৈরি করলেন। সেই নির্যাস খাওয়ানো হলো বেরিবেরি আক্রান্ত কুকুরকে । কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কুকরটা সুস্থ হয়ে উঠছে। তাঁর মানে আইকম্যানের ধারণাই ঠিক, উইলিয়ামসের গবেষণাও ঠিকঠাক পথেই এগুচ্ছে। এরপর সেই নির্যাস খাওয়ানো হলো বেরিবেরি আক্রান্ত মানুষকেও। তারাও সুস্থ হয়ে উঠল।
সবচেয় ভালো ফল পাওয়া গেল শিশুদের ক্ষেত্রে। বেরিবেরিতে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত শিশুদের খাওয়ানো হলো সেই নির্যাস। মাত্র তিনঘণ্টার মধ্যে শিশুরা সুস্থ হয়ে উঠল। সুতরাং উইলিয়ামস তখন শতভাগ নিশ্চিত—চালের লাল আবরণে এমন এক উপাদান আছে, যেটার অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।
তারপর প্রচুর গবেষণা আর কাঠখড় পুড়িয়ে সেই উপদানটা শনাক্ত করতে সক্ষম হলেন উইলিয়ামস আর তার সহযোগী চিকিৎসকেরা। সেটা ছিল থায়ামিন। এখন যেটাকে ভিটামিন বি ১ বলে। এভাবেই ১৯৩৪ সালে ইতিহাসের প্রথম ভিটামিনটা আবিষ্কার করেন রবার্ট উইলিয়ামস।
সূত্র : ব্রিটানিকা, কালের কন্ঠ
এফএইচ/বিডি
CBNA24 রকমারি সংবাদের সমাহার দেখতে হলে
আমাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করতে ক্লিক করুন।
আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করতে পোস্ট করুন।